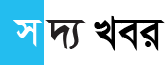এম এ মাসুম
বিশ্লেষণ
ডলারের স্থিতিশীলতায় ক্রলিং পেগ কতটা সহায়ক

প্রায় দুই বছর ধরে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিশেষ করে ডলার-সংকট কোনোভাবেই কাটছে না। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর মার্চ মাস থেকে দেশে ডলারের দাম বাড়তে থাকে। শুরুতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরামর্শেই ডলারের দাম বাড়ানো বা কমানো হতো। এতে আইএমএফ আপত্তি করলে ডলারের দাম নির্ধারণের বিষয়টি বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) ও অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশের (এবিবি) ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতেও ডলারের দাম নির্ধারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপ ছিল। গত বছরের জুলাইয়ে মুদ্রানীতি ঘোষণার সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলারের দাম নির্ধারণে ক্রলিং পেগ পদ্ধতি চালুর ঘোষণা দেওয়া হয়।
মুদ্রার বিনিময় হার হলো এমন একটি হার, যার মাধ্যমে একটি মুদ্রা অন্য মুদ্রার সঙ্গে বিনিময় করা হয়। বিনিময় হার ব্যবস্থা একটি দেশের মুদ্রানীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তিনটি মৌলিক ধরনের বিনিময় ব্যবস্থা রয়েছে : ভাসমান, স্থায়ী ও পেগড ফ্লোট এক্সচেঞ্জ। অধিকাংশ অনেক দেশে ডলারের মান সম্পূর্ণ বাজারমুখী রাখতে এবং হস্তক্ষেপবিহীন মান নির্ধারণে ‘ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট’ বা ভাসমান হার ব্যবহার করা হয়। এতে বাজারে চাহিদা ও অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডলারের দাম ওঠানামা করে।
চলতি বছরের ১৭ জানুয়ারি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন) নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন মুদ্রানীতিতে মার্কিন ডলারের দাম নির্ধারণে ‘ক্রলিং পেগ’ পদ্ধতি চালুর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর ধারাবাহিকতায় ৮ মে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মার্কিন ডলারের ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রলিং পেগ এক্সচেঞ্জ রেটপদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে মার্কিন ডলারের দাম ক্রলিং পেগ মিড রেট (সিপিএমআর) নির্ধারণ করা হয়েছে ১১৭ টাকা। ফলে তফসিলি ব্যাংকগুলো সিপিএমআরের আশপাশে মার্কিন ডলার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে এবং আন্তব্যাংক লেনদেন করতে পারবে।
মূলত নিয়ন্ত্রিত বা বেঁধে দেওয়া বিনিময় হার থেকে উন্মুক্ত বাজার দরে প্রবেশের আগের ধাপটিই মূলত ‘ক্রলিং পেগ’। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যবহারের ভিত্তিতে ক্রলিং পেগকে দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা- অ্যাকটিভ ও পেসিভ পেগ। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের উচ্চ ও নিম্নসীমার একটি ব্যান্ড বেঁধে দিলে তাকে অ্যাকটিভ ক্রলিং বলা হয়। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতির হার পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়ের হার নির্ধারণ করা হলে তাকে পেসিভ ক্রলিং বলা হয়। এর প্রাথমিক লক্ষ্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ করা। ক্রলিং পেগ সিস্টেমের অনেক ঝুঁকি রয়েছে যেমন : কৃত্রিম বিনিময় হার তৈরি হয়; ফটকাবাজ, ফরেক্স ব্যবসায়ী এবং বাজারে ঝুঁকি তৈরি করে, যা মুদ্রা বিনিময়কে অস্থিতিশীল করে তোলে। অন্যদিকে ক্রলিং পেগির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপ ও কারসাজির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেতে পারে।
বাজার স্থিতিশীল করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ‘ক্রলিং পেগ’ নীতি অনুসরণের ঘোষণা দিলেও বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা ভিন্ন তথ্যই দিচ্ছে। আইএমএফের তথ্যানুসারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন বলিভিয়া, নিকারাগুয়া, সলমন দীপপুঞ্জ, তিউনিসিয়া ক্রলিং পেগ পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। অন্যদিকে বেলারুশ, হুন্ডুরাজ, ইসরায়েল, রুমানিয়া ও স্লোভানিয়া বেন্ডের আওতায় ক্রলিং পেগপদ্ধতি অনুসরণ করেছে। চীনের ভিন্ননীতির কারণে নিকারাগুয়া এবং ভিয়েতনাম ক্রলিং পেগপদ্ধতি ব্যবহার করে, যাকে অনেকটা ‘বিলম্বিত পেগ’ বলে অভিহিত করা হয়। একসময় বতসোয়ানা, আর্জেন্টিনা, ইকুয়েডর, উরুগুয়ে এবং কোস্টারিকার মতো দেশগুলো পরীক্ষামূলক ক্রলিং পেগনীতি অনুসরণ করলেও পরে তা পরিত্যাগ করে। এ নীতি অনুসরণ করে ইসরায়েল যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছে। থাইল্যান্ডও একসময় এটি অনুসরণ করেছিল। আবার বিশ্বের অনেক দেশই এ পদ্ধতিতে সুবিধা করতে পারেনি। এরই মধ্যে আবার অনেক দেশ এ নীতি থেকে বের হয়েও এসেছে। সম্প্রতি এ নীতি অনুসরণের ঘোষণা দিয়েছে নাইজেরিয়া। দেশটির স্থানীয় মুদ্রা ‘নাইজেরিয়ান নাইরা’-এর বিনিময় হার নিয়ে অস্থিরতা চলছে। ব্যাংক খাতের সঙ্গে কালোবাজারে ডলারের বিপরীতে নাইরার বিনিময় হার প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৮৮ সালে মেক্সিকান কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের মুদ্রা পেসোকে ডলারের সঙ্গে পেগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে অপ্রত্যাশিত এক ঘোষণায় মেক্সিকোর মুদ্রা পেসোর অবমূল্যায়ন ঘোষণা করে এবং পরীক্ষামূলক ক্রলিং পেগিং বিনিময় হার চালু করে, কিন্তু প্রত্যাশিত ফলাফল পেতে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু এ পদ্ধতি দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিশীলতা অর্জন এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরো কঠিন করে তোলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণ ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৫ হাজার কোটি ডলার ‘বেইল আউট’ ঋণ নিতে হয় মেক্সিকো সরকারকে। আর্জেন্টিনায় ইউএস ডলার দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। ২০১৯ সালে আর্জেন্টিনায় ১ ডলারে ৩৭ পেসো এবং ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ১৮৩ পেসো পাওয়া যেতে। কিন্তু তিন মাস না যেতেই ক্রলিং পেগনীতি পুরোপুরি মুখ থুবড়ে পড়ে। দেশটির খুচরা ও কালোবাজারে প্রতি ডলারের বিপরীতে পাওয়া যেত প্রায় দ্বিগুণ অর্থ। ২০২৩ সালের আগস্টের মাঝামাঝিতে আর্জেন্টিনা ডলারের বিনিময় হারকে পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে না দিয়ে ‘ক্রলিং পেগ’ নীতি গ্রহণ করে এবং প্রতি ডলারের দাম নির্ধারণ করা হয় ৩৫০-৩৫৫ পেসো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডলারে মূল্য ৮০০ পেসো ছাড়িয়ে যায় এবং ক্রলিং পেগনীতি ব্যর্থ হয়।
তাত্ত্বিকভাবে বৈদেশিক মুদ্রাবাজার থাকবে বাংলাদেশ ব্যাংকের হস্তক্ষেপমুক্ত। যদিও তখনো মুদ্রাবিনিময় হার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতেই থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব সময়ই এতে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ রেখে আসছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক এ ব্যাপারে অনুসরণ করে আসছে ‘ম্যানেজড ফ্লোটিং রেট’নীতি। প্রকৃতপক্ষে টাকাকে কখনোই পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়নি বাংলাদেশ ব্যাংক। কার্যত নিজের হাতেই রেখে দিয়েছে মুদ্রাবিনিময় হার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। আর এ কাজটি করেছে আন্তব্যাংক বাজারের রেট নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। বাংলাদেশের রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক সব সময়ই টাকার মান ধরে রাখতে চেয়েছে।
অর্থনীতিবিদরা বলছেন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সময়ে কোনো দেশে ‘ক্রলিং পেগ’নীতি অনুসরণ করা হলে সেটির ফল পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো দেশের রিজার্ভ দুর্বল হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বিনিময় হারের অস্থিরতা বেড়ে গেলে এবং একই সঙ্গে উচ্চ মূল্যস্ফীতি চলমান থাকলে সেখানে এ নীতি কাজ করে না। বরং এটি বিনিময় হারের অস্থিরতাকে আরো উসকে দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি। পাশাপাশি হুন্ডির বাজারকে আরো বেশি শক্তিশালী করে তুলতে ভূমিকা রাখে। ডলারের সংকট বিদ্যমান অবস্থায় থাকলে ক্রলিং পেগ কিছুটা সুফল দিতে পারে। কিন্তু সংকট বেড়ে গেলে এ নীতির অনুসরণ কোনো কাজে আসবে না। এ নীতি কোনো দেশে সফল হয়েছে, সেটিও তেমন ইতিহাস পাওয়া যায় না। বাস্তবতা হলো ক্রলিং পেগ ডলার-সংকটকে স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক করার একটি অস্থায়ী পদ্ধতি। আমি মনে করি ডলারকে পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। তাহলে ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাড়তে থাকবে। একদিকে ঋণের সুদের হার বৃদ্ধির ফলে ভোক্তাপর্যায়েও মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে।
তা ছাড়া শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল, ক্যাপিটাল মেশিনারিজ, মধ্যবর্তী পণ্য ইত্যাদিসহ সব ধরনের পণ্যের আমদানিব্যয় ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে। ফলে একদিকে মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী হবে, অন্যদিকে কর্মসংস্থান মারাত্মকভাবে হ্রাস পাবে। সুদহার ও ডলারের দাম উভয় বৃদ্ধির ফলে দেশের বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির চাপ সহ্য করতে পারবে না। এ কারণে বাংলাদেশের মতো অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকার সব সময়ই ডলারের ওপর কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে, বাংলাদেশকেও এ নিয়ন্ত্রণ অন্তত আরো কয়েক বছর রাখতে হবে।
শুধু নীতি পরিবর্তন করে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান দুই উৎস রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহে স্থবিরতা চলছে। অন্যদিকে খেলাপি ঋণ পাহাড়সহ হচ্ছে। গত বছর আয়োজিত তৃতীয় গ্লোবাল বিজনেস সামিটে বলা হয় ৬০ শতাংশ রেমিট্যান্স আসে হুন্ডির মাধ্যমে। বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশ থেকে হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচার উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশ থেকে কতভাবে অর্থ পাচার হয় তা বহুল আলোচিত। হুন্ডি ও পাচারের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা না নিলে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে না। সেই সঙ্গে ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধেও সরকারকে কঠোর হতে হবে। তবে ডলার-সংকট স্থায়ীভাবে কাটাতে রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধির বিকল্প নেই।
লেখক : ব্যাংকার ও ‘বৈদেশিক বিনিময় বাণিজ্য ও অর্থায়ন’ গ্রন্থের লেখক
"