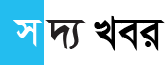এস এম সুলতান
মৃত্তিকা সমর্পিত শিল্পী
ড. আফরোজা পারভীন

চিত্রকর এস এম সুলতানের পুরো নাম শেখ মোহাম্মদ সুলতান। সুলতান নামেই সমধিক পরিচিত। ডাকনাম লাল মিয়া। আত্মবিশ্বাসী, আড়ালচারী ও ক্ষণজন্মা। তার শিল্পচেতনায় মূল উপজীব্য প্রকৃতি-পরিবেশ ও মানুষ। আর তারই অনুষঙ্গ ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ ও সংগ্রাম। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষমাত্রই শক্তিময়। সকল শক্তির আধার তারা। তাদের অস্থিমজ্জায় পুঞ্জীভূত অঢেল প্রাণরস। শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি ছিল তার পক্ষপাত। কারণ তারাই চালায় অর্থনীতির চাকা। তাদের শ্রমে ঘামে নির্মিত হয় উন্নয়ন বা সভ্যতা। তার জীবনের মূল সুরটি তাই বাঁধা ছিল গ্রামীণ জীবন, কৃষক ও কৃষিকাজের সঙ্গে। বাঙালির দ্রোহ, প্রতিবাদ, সংগ্রাম, প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকার ইতিহাস এবং অনুপ্রেরণা গ্রাম। তাই তিনি কৃষক পুরুষের শরীরকে করেছেন পেশিবহুল ও বলশালী, কৃষক রমণীর শরীরকে এঁকেছেন সুডৌল ও সুঠাম গড়নে, তাকে দিয়েছেন যুগপৎ লাবণ্য ও শক্তি। তার ছবিতে কখনো কৃশকায় মানুষ দেখা যায় না, দেখা যায় পেশিবহুল স্বাস্থ্যবান অবয়ব। কেন? সে জিজ্ঞাসার জবাব তার নিজের জীবন।
১৯২৩ সালের ১০ আগস্ট। চিত্রাবিধৌত তেভাগা কৃষক আর নীলবিদ্রোহের স্মৃতিধন্য নড়াইলের মাছিমদিয়া গ্রামে জন্ম সুলতানের। পিতা মেছের আলি রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। স্ত্রী, ছেলে লাল মিয়া ও মেয়ে ফুলমণিকে নিয়ে তার সংসার। মেছেরের একার উপার্জনে সংসার চলে। স্ত্রী হঠাৎ মারা যান। মেছের দ্বিতীয় বিয়ে করেন আয়াতুন্নেসাকে। রাজমিস্ত্রির কাজ করে মেছের যা আয় করেন, তার পরিমাণ খুব সামান্য। সংসারের অভাবের যন্ত্রণার সঙ্গে বাড়তি যোগ হয় লাল মিয়ার ওপর সৎ মায়ের অত্যাচার।
অভাব সত্ত্বেও তার পিতা লালমিয়াকে ১৯২৮ সালে নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করে দেন। কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে পড়াশোনা করার সৌভাগ্য হয়নি সুলতানের। বাবার সঙ্গে রাজমিস্ত্রির কাজ শুরু করেন। জীবনের শুরুতেই তাকে পেশিতে নির্ভর করে নির্বাহ করতে হয়েছে জীবিকা। লড়াই করতে হয়েছে দৈনন্দিন দারিদ্র্যের সঙ্গে। এ লড়াইয়ের জন্য কোমল পেশিতে সঞ্চার করতে হয়েছে শক্তি ও সাহস। পরবর্তী সময়ে তিনি যে মানুষকে শক্তিমান ও মহীয়ান করে চিত্রিত করেছেন, তা নিছক শিল্প নয়, ঘনিষ্ঠ জীবনবোধ ও সমাজ বাস্তবতারও বহিঃপ্রকাশ। কেন তার পুরুষরা পেশিবহুল, নারীরা শক্তিমত্তÑ সে প্রশ্নেরও জবাব।
জীবনবাদী শিল্পী সুলতান বলেন, ‘আমি আমার বিশ্বাসের কথা বলছি। আমার সকল চিন্তা, সবটুকু মেধা, সবটুকু শ্রম দিয়ে যা কিছু নির্মাণ করি, তা কেবল মানুষের জন্য, জীবনের জন্য, সুন্দর থেকে সুন্দরতম অবস্থায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য। আমার ছবির মানুষরা, এরা তো মাটির মানুষ, মাটির সঙ্গে স্ট্রাগল করেই এরা বেঁচে থাকে। এদের শরীর যদি শুকনো থাকে, মনটা রোগা হয়, তাহলে এই যে কোটি কোটি টন মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু সকল আসে কোত্থেকে? ওদের হাতেই তো এসবের জন্ম। শুকনো, শক্তিহীন শরীর হলে মাটির নিচে লাঙলটাই দাববে না এক ইঞ্চি। আসলে, মূল ব্যাপারটা হচ্ছে এনার্জি, সেটাই তো দরকার। ওই যে কৃষক, ওদের শরীরের অ্যানাটমি আর আমাদের ফিগারের অ্যানাটমি, দুটো দুই রকম। ওদের মাসল যদি অত শক্তিশালী না হয়, তাহলে দেশটা দাঁড়িয়ে আছে কার ওপর? ওই পেশির ওপরেই তো আজকের টোটাল সভ্যতা।’
সুলতানের ছবিতে পরিপূর্ণতা এবং প্রাণপ্রাচুর্যের পাশাপাশি আছে শ্রেণির দ্বন্দ্ব এবং গ্রামীণ অর্থনীতির কিছু ক্রুর বাস্তবতার চিত্রও। হত্যাযজ্ঞ (১৯৮৭) ও চরদখল (১৯৮৮) এ রকম দুটি ছবি।
লাল মিয়া ছিলেন সুরসাধক। চমৎকার বাঁশি বাজাতেন। নড়াইলের জমিদার বাড়ির পুকুর ঘাট, স্কুলের অনুষ্ঠান ছাড়াও বনেবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বাঁশি বাজাতেন তিনি। এমন কথাও শোনা গেছে, জমিদার বাড়ির পুকুর ঘাটে লাল মিয়া বাঁশি বাজানোর সময় কালো কেউটে সাপ দুই পাশে নাচত।
বাবার কাজে সহযোগিতা করার জন্য প্রায়ই জমিদার বাড়ি যেতেন লাল মিয়া। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছবি আঁকতেন। জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায়বাহাদুর ও তার শিল্পরসিক ছোটভাই লাল মিয়ার ছবি আঁকার নেশার কথা জানতেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন সুলতান। ১৯৩৮ সালে সৎ মায়ের সঙ্গে রাগারাগি করে কলকাতা যান তিনি। কলকাতায় গিয়ে জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়িতেই ওঠেন। ধীরেন্দ্রনাথ লাল মিয়াকে বিলেত থেকে ছবি আঁকার বিভিন্ন স্কেচের দুটো বই এনে দিয়ে বললেন, ‘লাল মিয়া, যদি ভালো করে ছবি আঁকা শিখতে চাস, তাহলে তোকে এই প্রাথমিক বিদ্যেগুলো শিখতে হবে।’ জমিদারের ছোটভাই এক দিন লাল মিয়াকে বললেন, ‘দেখো লাল মিয়া, বড় শিল্পী হতে হলে তোমাকে আর্ট স্কুলে বা কলেজে ভর্তি হতে হবে। তার আগে তোমাকে ইন্টারভিউ দিতে হবে এবং ইন্টারভিউ দিয়ে পাসও করতে হবে।’
সে সময় কলকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অন্তত এন্ট্রান্স (মেট্রিক) পাশের যোগ্যতা প্রয়োজন হতো। সে যোগ্যতা লাল মিয়ার ছিল না। লাল মিয়ার আর্ট কলেজে পরীক্ষা দেওয়া যখন অনিশ্চিত, তখন জমিদার বাবু বললেন, ‘একটা উপায় অবশ্য আছে। শাহেদ সোহরাওয়ার্দীকে ধরতে হবে। তিনি এই কলেজের ভর্তি কমিটির সদস্য। তিনি বলে দিলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না।’ সোহরাওয়ার্দীর সহযোগিতায় আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে যান সুলতান ১৯৪১ সালে। ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হন। শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর বাড়িতে থেকেই কলেজে যেতেন। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন আর্টের অসাধারণ সমঝদার ও সমালোচক। তার বিশাল লাইব্রেরি জুড়ে ছিল বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকরদের শিল্পকর্ম আর সেরা সেরা সমালোচকের বই পুস্তক। সোহরাওয়ার্দী পরিবারে থাকার কারণেই আরবি, ফারসি ও ইংরেজিতে বেশ দক্ষ হয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু চার বছরের মাথায় জেগে ওঠে সুলতানের বোহেমিয়ান সত্তা। জেগে ওঠে মাছিমদিয়ার দুরন্ত লালমিয়া। টান পড়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার। ১৯৪৪ সাল। সুলতান সব পেছনে ফেলে এক দিন কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে দিল্লি, দিল্লি থেকে লখনৌ, সেখান থেকে হিমালয়ের পাদদেশ। তার ভবঘুরে শিল্পীজীবন কাটতে লাগল ঘুরে ঘুরে। কন্যাকুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষ চষে বেড়ান তিনি।
তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। ছোট-বড় শহরগুলোতে ইংরেজ ও আমেরিকান সৈন্যদের ছবি এঁকে বিক্রি করে জীবন ধারণ করেছেন এবং প্রদর্শনীও করেছেন। সুন্দরের প্রতি সুতীব্র টান আর ছুটে চলার আনন্দে ছুটছেন তিনি। এরপর কাশ্মীরের উপজাতীয়দের সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। মিসেস হাডসন নামে কানাডীয় এক মহিলার উদ্যোগে ১৯৪৫ সালে ভারতের সিমলাতে সুলতানের প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী হয়। সেখানকার মহারাজা প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন। এরপর সুলতান চলে যান পশ্চিম পাকিস্তানে।
দেশ বিভাগের পর সুলতান কিছুদিনের জন্য দেশে ফেরেন। ১৯৫০ সালে চিত্রশিল্পীদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি আমেরিকা যান। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, শিকাগো, বোস্টন এবং এরপর লন্ডনে তার ছবির প্রদর্শনী হয়। সুলতানের চরিত্রে ছিল পার্থিব বিষয়ের প্রতি অনীহা এবং কোনো এক স্থানে শিকড় ছড়িয়ে বসার প্রতি তীব্র অনাগ্রহ। তাই তখনকার আঁকা ছবির নমুনা, এমনকি ফটোগ্রাফও এখন আর নেই।
শিশুদের নিয়ে সুলতানের অনেক স্বপ্ন ছিল। ১৯৫৩ সালে নড়াইল ফিরে তিনি ‘শিশুস্বর্গ’ ও ‘চারুপীঠ’ ‘নন্দন কানন’ প্রাইমারি, একটি হাইস্কুল এবং একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সে স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন।
১৯৭৬ সাল পর্যন্ত সুলতান শিল্পরসিকদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যান। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি তার ছবির এক প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এ প্রদর্শনীটিই তাকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়।
তার ছবিতে গ্রাম সৃষ্টির কেন্দ্র, কৃষকই প্রকৃত জীবনশিল্পী। এজন্য কৃষক ও কৃষকের জীবন কিংবদন্তিতুল্য শক্তি নিয়ে উপস্থিত তার ছবিতে। তার কাজে অবয়বধর্মিতাই প্রধান। তিনি আধুনিক, বিমূর্ত শিল্পের চর্চা করেননি; তার আধুনিকতা ছিল জীবনের শাশ্বতবোধ ও শিকড়ের শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা। তিনি ফর্মের নিরীক্ষাকে গুরুত্ব দেননি, দিয়েছেন মানুষের ভেতরের শক্তির উত্থানকে, ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই এবং ঔপনিবেশিকোত্তর সংগ্রামের নানা প্রকাশকে।
তার স্টাইল অননুকরণীয়। তাই তার কোনো অনুসারী বা স্কুল নেই। কারণ তার মতো মৃত্তিকা সমর্পিত জীবন আর কোনো শিল্পী যাপন করেননি। সুলতান তেলরং ও জলরঙে ছবি এঁকেছেন, ব্যবহার করেছেন সাধারণ কাগজ, সাধারণ রং ও চটের ক্যানভাস। এজন্য তার অনেক ছবির রং নষ্ট হয়ে গেছে।
আশির দশক থেকে সুলতান নড়াইলেই বসবাস করেছিলেন। তার বাড়িটি আশ্রয় নেওয়া মানুষ, শিশু এবং জীবজন্তুর জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। একটি চিড়িয়াখানা ছিল তার। শিশুদের জন্য একটি বিরাট নৌকাও বানিয়েছিলেন।
শেষ জীবনে অসুস্থ সুলতানের ছবির কদর অনেক বেশি ছিল। কিন্তু অনেকেই ছবি নিয়ে অথবা বিক্রি করে টাকা দিত না। সে কারণে সংসারে দিন দিন সংকট বাড়তে থাকে। সুলতান ‘শিশুস্বর্গ’ ও শিশুদের নিয়ে দিনরাত উৎকণ্ঠায় থাকতেন। ইচ্ছা থাকলেও তাই আর ভবঘুরে হতে পারেননি। কারণ বিশাল এক সংসারের দায়িত্ব তখন তার কাঁধে। তা ছাড়া নব্বইয়ের দশকের শুরুতেই সুলতানের শরীর ভেঙে পড়েছিল।
১৯৮২ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুলতানকে ‘এশিয়ার ব্যক্তিত্ব’ হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৮৭ সালে ঢাকার গ্যোটে ইনস্টিটিউটে সুলতানের ছবির একটি প্রদর্শনী হয়। ১৯৯৪ সালে ঢাকার ‘গ্যালারি টোনে’ সুলতানের স্কেচ নিয়ে একক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীটি ছিল সুলতানের জীবনের শেষ প্রদর্শনী।
১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর যশোরের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মহান এই শিল্পীর জীবনাবসান ঘটে। মৃত্তিকা সমর্পিত এই অমর শিল্পীর প্রতি অতল শ্রদ্ধা।
"