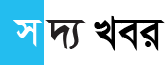মো. রেজাউল করিম
জন্মদিনে শ্রদ্ধা : নজরুলসংগীতে প্রেমিকসত্তা

কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার রচিত সংগীতে সর্বজনীন প্রেমের যে জয়গান গেয়েছেন, বাংলা ভাষায় তেমন চিহ্ন আর কেউ রাখতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।
নজরুল রচিত চার হাজার সংগীত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি অমর প্রেম-উৎসারিত হয়েছে তার প্রেমিকসত্তা থেকে। প্রাথমিক স্তরে নজরুলের সংগীত সাহিত্যের বিস্তরণ ঘটেছে কাব্য-সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি মানববন্দনা, দেশবন্দনা, গণসংগীত, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গানের মধ্য দিয়ে। পরে বাংলা গজল রচনা ও পরিবেশনকালে নজরুল আবির্ভূত হয়েছেন নবরূপে, ভিন্ন আঙ্গিকে। এই পর্যায়ে তিনি ইসলামি সংগীত—হামদ, নাত, হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির সংগীত এমনকি শ্যামাসংগীতেও মগ্ন হয়ে ওঠেন। তিনি ইসলামি সংগীত, শ্যামাসংগীত, শাক্ত, শৈব, ভজন, কীর্তন, বাউল-ভাটিয়ালি, গণসংগীত, আধুনিক গান ও হিন্দু-মুসলিমের মিলনপ্রত্যাশী অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক গান রচনা করে সংগীতের সব শাখায় অবাধে বিচরণ করেছেন। নজরুল রচিত সংগীত খণ্ডিত বা ক্ষুদ্রচিন্তায় বিবেচনা না বরং বৃহৎ ক্যানভাসে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংগীত-সাহিত্যে তিনি জাতপাতের ঊর্ধ্বে এমন এক প্রেমিক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, যা উপমহাদেশে বিরল। সংগীত রচনায় তিনি ছিলেন প্রবহমান ঝরনাধারার মতো—খরস্রোতা স্রোতস্বিনী।
পৃথিবীতে রয়েছে অসংখ্য ধর্ম। কোনো ধর্মের বিস্তার প্রধানত একটি অঞ্চলে একটি নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। আবার কিছু ধর্মের বিস্তার পৃথিবীব্যাপী—যেমন ইসলাম, খ্রিস্ট, হিন্দু ও বৌদ্ধ। কবি নজরুল যে জনপদের মানুষ ছিলেন, সেই জনপদ বিশেষত ইসলাম ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বসবাসস্থল হওয়ায় সম্ভবত তিনি তার সংগীতে এই দুই ধর্মের স্রষ্টা, প্রবর্তক, দর্শন ও বিশ্বাসকে অনুষঙ্গ হিসেবে সর্বজনীনতার স্বাক্ষর রেখেছেন।
নজরুলের ইসলামি সংগীত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি ইসলামের মৌলিক আকিদার অনুসারী নন, বরং উপমহাদেশে বিস্তৃত ইসলাম ধর্মের সুফিবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সংগীত রচনা করেছেন। যেমন : তিনি লিখেছেন, ‘খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই প’ড়ে/ছেড়ে’ মস্জিদ আমার মুর্শিদ এল যে এই পথ ধ’রে।’ সর্বশক্তিমান মহাজগতের স্রষ্টা ‘আল্লাহ’কে কবি নজরুল প্রভু এবং নিজেকে প্রভুর ভৃত্য না ভেবে বরং প্রেমিক ভেবেছেন। যে কারণে লিখেছেন খোদার প্রমের শরাব পিয়ে (পান করে) তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। (যদিও ইসলামের মৌলিক আকিদানুসারে শরাব পান ও তার দরুন বেহুঁশ হওয়া কোনোটাই অনুমোদিত না)। তিনি সুফি-সাধকদের মতো ইসলামের সর্বশেষ নবীকে মুর্শিদণ্ডরূপে অন্তরে ধারণ করে খোদা তথা আল্লাহর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের স্বাক্ষর রাখতে চেয়েছেন। নজরুলের ইসলামি নাতগুলো যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা তার বিশ্বাসজাত বলেই প্রতীয়মান হয়। যেমন লিখেছেন, খোদা এই গরীবের শোন শোন মোনাজাত।/দিও তৃষ্ণা পেলে ঠান্ডা পানি ক্ষুধা পেলে লবণ-ভাত।/মাঠে সোনার ফসল দিও,/দিও গৃহ ভরা বন্ধু প্রিয়, দিও/হৃদয় ভরা শান্তি দিও- (খোদা) সেই তো আমার আবহায়াত।’ (এমন পানি, যা মানুষ পান করলে চিরজীবী হবে। বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই। - লেখক)।
সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও বিশ্বাস থেকে তিনি শেষ বিচারের দিন প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘সেদিন নাকি তোমার ভীষণ কাহ্হার রূপ দেখে/পীর পয়গম্বর কাঁদবে ভয়ে “ইয়া নফসী” ডেকে/...আমি তোমায় দেখে হাজারবার দোজখ যেতে রাজী।’ আবার আল্লাহর অচিন্তনীয় রহমত প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘যেরূপে হোক বারেক যদি দেখে তোমায় কেহ/দোজখ কি আর ছুঁতে পারে পবিত্র তাঁর দেহ।/সে হোক না কেন হাজার পাপী হোক না বে-নামাজী।’
নজরুল রচিত সংগীতে সুফিবাদের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি তার ভালোবাসাও শাম্বত। মুর্শিদ আরবি শব্দ, যার অর্থ পথপ্রদর্শক বা শিক্ষক। সুফিবাদে এটাকে আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হিসেবে বোঝানো হয়। শব্দটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয় কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া, চিশতিয়া ইত্যাদি তরিকায়। তিনি লিখেছেন, ‘তৌহিদেরি মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম।/ঐ নাম জপলেই বুঝতে পারি খোদায়ী কালাম—/মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম।/ঐ নামেরি রশি ধ’রে যাই আল্লার পথে,/ঐ নামেরি ভেলা ধ’রে ভাসি নূরের স্রোতে,/ঐ নামেরি বাতি জ্বেলে দেখি আরশের মোকাম।/মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম।’ এখানেও নজরুল উপমহাদেশে প্রসারিত ইসলামি সুফিবাদের দ্বেতবাদী সত্তায় প্রভাবিত হয়েছেন, যদিও মূল ইসলাম অদ্বৈতবাদী সত্তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত।
বাংলা গজল কাজী নজরুল ইসলামের অমর সৃষ্টি। বাংলা গজলে তিনি খোদার কাছে পৌঁছানোর জন্য নবীপ্রেমে মশগুল হয়েছেন। নজরুল ব্যক্তি হিসেবেও ছিলেন মানবতাবাদী। তিনি ছিলেন মূলত প্রেমচেতনায় বিশ্বাসী মানব। তাই তার সাহিত্যের মূল ক্ষেত্র কবিতা ও গানে স্রষ্টা ও মানুষের প্রতি প্রেম প্রতিফলিত হয়েছে। তার কবিতা ও গান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্রষ্টা ও মানুষের প্রতি প্রেম ছত্রে ছত্রে উৎসারিত হয়েছে।
গজল রচনায় বহুভাষী নজরুল ফারসি গজলকেই প্রেরণার উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছেন। গজল এমন এক সংগীত, যেখানে উল্লিখিত অর্থের ভেতরে থাকে গূঢ় অর্থ। যেমন শরাব, পাখি, ফুল, নদী, ঝরনার স্রোতস্বিনী বস্তুগত জগতের এসব শব্দ গজলে মূলত রূপক হিসেবে উপস্থাপিত হয়। ইহলৌকিক জগতের উপমাগুলো ব্যবহার করে পারলৌকিক জগতের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করাই গজলের মূল নান্দনিক রূপ। গজলে রচয়িতা অদ্বৈত পরমসত্তা বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার বিরহ-মিলনের অদম্য অথচ অনুভবনীয় বাণী তৈরি করেন। ফারসি গজলের মূলভাব ঐশী প্রেম, যেখানে হৃদয় হচ্ছে সেই পাত্র, যে-পাত্রে স্থান করে নেওয়ার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন, তা হচ্ছে নিবিষ্ট প্রেম। বাংলা গজল রচনাকালে কবি নজরুল ফার্সি গজলের মূলভাব প্রেমকে অবলম্বন করে অদ্বৈত সত্তার বন্দনায় সব ধর্মের সাধক ও প্রেমিক মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। কবি নজরুলের বাংলা গজলেও তাই পরমাত্মা-জীবাত্মার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ও টানপড়েন বিবৃত হয়েছে। এসব গজলে মানবীয় প্রেম যেন বস্তুগত বা জাগতিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমে রূপ নিয়েছে। তাই তিনি বলেছেন, ‘প্রেম আসে ঘুমঘোরে। ঘুম ভেঙে বিচ্ছেদ রূপ নেয় কান্নায়।’ আবার লিখেছেন, ‘এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি/খোদা তোমার মেহেরবানি।/শস্যশ্যামল ফসলভরা/মাঠের ডালিখানি/খোদা তোমার মেহেরবানি।’
কবি নজরুলের আর এক সংগীত-কীর্তি শ্যামাসংগীত। কবি নজরুল আড়াই শতাধিক শ্যামাসংগীত রচনা করেন। শ্যাম অর্থাৎ (প্রায়) কালো এবং শ্যামার নারীরূপ—শ্যামা; নজরুলের খ্যাতির এক বিশেষ এক কারণ শ্যামাসংগীত রচনা। শ্যাম অর্থাৎ কালো এবং এর নারীরূপ হলো শ্যামা। হিন্দুধর্মে শ্যামা বা কালী একজন পূজনীয় দেবী, তাকে উদ্দেশ্য করে যে সংগীত রচিত হয়, তা-ই শ্যামাসংগীত নামে পরিচিত। সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেনের পরে নজরুলই একমাত্র গীতিকার, যিনি এত অধিকসংখ্যক শ্যামাসংগীত রচনা করেন। এ জন্য তিনি নন্দিত ও নিন্দিতও হয়েছেন। শ্যামাসংগীত রচনার পরে তিনি ‘কাফির’ উপাধিও লাভ করেন। তবে কবি নজরুল গীতিকার হিসেবে স্বীয় গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না।
শ্যামাসংগীত রচনায় তিনি যে অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তা দুর্লভ। প্রতিটি গানে তিনি কী অসাধারণ শব্দবিন্যাস করেছেন। অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও হিন্দুদের আরাধ্যা একজন দেবীর যে গুণকীর্তন করেছেন, তা শুধু সংগীত রচনা কৌশল এবং ভাষায় দখল থাকলেই হয় না—বরং প্রয়োজন আত্মিক একাত্মতা- যা তার রচিত শ্যামাসংগীতে দেখা যায়। ‘আমায় আঘাত যত হানবি শ্যামা ডাকব তত তোরে।/মায়ের ভয়ে শিশু যেমন লুকায় মায়ের ক্রোড়ে।/ওমা চারধারে মোর দুখের পাথার/তুই পরখ্ কত করবি মা আর,/আমি জানি তবু পার হ’ব মা চরণতরী ধ’রে।’ কিংবা ‘ভক্তি, আমার ধুপের মত,/ঊর্ধ্বে উঠে অবিরত।/শিবলোকের দেব দেউলে,/মা’র শ্রীচরণ পরশিতে।’
সাহিত্যজীবনের প্রাথমিক স্তরে আলেমদের সঙ্গে তার চরম মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব দেখা যায়। আলেমদের কটাক্ষ করে ‘মোল্লা-মুন্সী’ অভিধায় অভিহিত করে তিনি বেশ কিছু কবিতাও লেখেন। সেই কাজী নজরুল তার সাহিত্যজীবনের শেষপর্যায়ে অর্থাৎ অসুস্থতার আগে কোরআনের কাব্যানুবাদ ‘কাব্য আমপারা’ রচনা করেন। লেখেন, ‘মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই/যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।’ কাফির কবি হলে ‘পরিত্যাজ্য’ আর ইসলামি কবি হলে ‘মাথার তাজ’—এ রকম মানসিকতা নিয়ে আর যাই হোক কাব্য-বিশ্লেষণ করা যায় না। নজরুলকে কাফির কবি বা ইসলামিক কবির গণ্ডিতে আবদ্ধ করা যায় না। শেষদিকে নজরুল রচিত অসংখ্য গজল, হামদ ও নাত উল্লেখ করে অনেকেই নজরুলকে ইসলামি কবির তকমায় আবদ্ধ করতে চান, যা অসংগত।
কবি নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা আমাদের মানবিক মূল্যবোধ উজ্জীবিত করে। আন্তসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দের মেলবন্ধন তৈরি করে। তার অমর সৃষ্টি ‘মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান’ এবং বিদ্রোহী কবিতায় তিনি মানবজাতির জন্য অসাম্প্রদায়িক, মানবিক এবং সৌহার্দ ও সম্প্রীতির বাণী রচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘গাহি সাম্যের গান—/মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান,/নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,/সব দেশে, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।’ অথবা ‘যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান/যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।’ আবার তিনি বক ধার্মিকদের বিরুদ্ধেও ছিলেন সোচ্চার। তাই তিনি লিখেছেন, ‘তব মসজিদ-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী, মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।’
বাস্তব কিছু ঘটনা প্রমাণ করে নজরুল দেবী কালীভক্তও ছিলেন। তার স্ত্রী জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তিনি কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (তারাশঙ্করও ছিলেন তন্ত্রসাধক) কাছে গিয়েও তান্ত্রিক সাধনাজাত ওষুধ নিয়ে আসেন। আবার তিনি মাজার-সংশ্লিষ্ট দরগায়ও একই উদ্দেশ্যে যান। শ্যামাসংগীতের দর্শন, তিনি অন্তর দিয়েই উপলব্ধি করেছিলেন বলে শুধু গান লিখেই ক্ষান্ত হননি বরং সেই গানে সুরারোপও করেছেন। ‘শ্মশানে জাগিছে শ্যামা মা’ গানটিতে কাজী সাহেব মালকোষ রাগাশ্রীত সুর করেছিলেন। এমন আরো শ্যামাসংগীতে তিনি সুরারোপ করেন। কেউ কেউ কবি নজরুলের দ্বিধর্মের প্রতি বিশ্বাসের কারণে তার দুর্বল ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ বলে অভিহিত করলেও এই লেখক ঘটনাকে প্যারাডক্সিক্যাল হিসেবে মনে করেন। তিনি হিন্দু-মুসলিমের জনপদে জন্মলাভ করেন। বাল্যকালে তিনি মক্তবে পড়াশোনা করেছেন। কিশোর বয়সে মাজারেও থেকেছেন। কিন্তু মানুষের স্বশিক্ষা পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে অতিক্রম করে। কবি নজরুল এমনই একজন মানুষ ছিলেন।
কবি নজরুলের কাব্য ও সংগীতে প্রেমচর্চায় প্রতীয়মান হয় যে, বুঝি-বা তার বিশ্বাস ছিল এক কথায় ‘প্যারাডক্সিকাল’। ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় তিনি লিখে গিয়েছেন, ‘আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা/করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা।’ তার কবি ও সংজ্ঞীতজ্ঞ জীবনে আপাতদৃষ্টিতে রয়েছে বৈপরীত্য। শ্যামাসংগীতে খ্যাতি অর্জন করে তিনি বাংলা ভাষায় যত ইসলামি সংগীত-গজল, হামদণ্ডনাত, ইসলামি কবিতা লিখেছেন, তা যেন বাংলা সংগীতে ইসলামি বিপ্লব। প্রশ্ন আসতে পারে, তিনি কি তাহলে অসুস্থতার আগে ‘ইসলামিস্ট’ হয়ে গিয়েছিলেন? তার উত্তর হচ্ছে, না। নজরুলচর্চায় অনেকেই যে ভুল করেন তা হচ্ছে, জাজমেন্টাল কনক্লুশান।
সব ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে বেরিয়ে তিনি যেভাবে সৃষ্টি ও স্রষ্টার বন্দনা করেছেন, তা তার মানবতাবাদী প্রেমিকসত্তা।