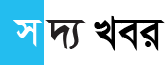ব্ল্যাক হোল-সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান

‘ব্ল্যাক হোল’ শব্দ দুটির সঙ্গে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। ১৯৬৯ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী জন হুইলার ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর শব্দটি সৃষ্টি করলেও এর চিন্তাধারার বয়স বস্তুত দু’শ’ বছরের। ভূতত্ত্ববিদ জন মিচেল তার লেখা একটি চিঠিতে ১৭৮৩ সালে রয়েল সোসাইটির সদস্য এবং বিজ্ঞানী হেনরি ক্যাভেন্ডিশকে এ সম্পর্কে জানান যে, ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর হলো বিপুল পরিমাণ ভর বিশিষ্ট কোনো বস্তু, যার মহাকর্ষের প্রভাবে আলোক তরঙ্গ পর্যন্ত পালাতে পারে না। কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কিত এ ধরনের মতামত ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকটভাবে উপেক্ষিত হয়। গত এক দশক ধরে এই কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে জোর বিতর্ক চলছে। তবে বর্তমানে অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীই এর অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন।
জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি অনুসারে, কৃষ্ণগহ্বর মহাকাশের এমন একটি বিশেষ স্থান যেখান থেকে কোনো কিছুই, এমনকি আলো পর্যন্ত, বের হয়ে আসতে পারে না। এটা তৈরি হয় খুবই বেশি পরিমাণ ঘনত্ব বিশিষ্ট ভর থেকে। কোনো অল্প স্থানে খুব বেশি পরিমাণ ভর একত্র হলে সেটা আর স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে না। আমরা মহাবিশ্বকে একটি সমতল পৃষ্ঠে কল্পনা করি। মহাবিশ্বকে চিন্তা করুন একটি বিশাল কাপড়ের টুকরো হিসেবে এবং তারপর যদি আপনি কাপড়ের ওপর কোনো কোনো স্থানে কিছু ভারী বস্তু রাখেন তাহলে কী দেখবেন? যেসব স্থানে ভারী বস্তু রয়েছে সেসব স্থানের কাপড় একটু নিচু হয়ে গেছে। এই একই ব্যাপার ঘটে মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে। যেসব স্থানে ভর অচিন্তনীয় পরিমাণ বেশি সেসব স্থানে নিচু হয়ে থাকার বদলে একেবারে গর্ত হয়ে যায়। এই ব্যাপক ভর এক স্থানে কু-লিত হয়ে স্থান-কাল-বক্রতার সৃষ্টি করে। প্রতিটি ছায়াপথের স্থানে স্থানে কম-বেশি কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সাধারণত বেশিরভাগ ছায়াপথই তার মধ্যস্থ কৃষ্ণগহ্বরকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মাণ।
সহজ ভাষায় ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর হলো অধিক ঘনত্ব ও ভর বিশিষ্ট এক প্রকার নক্ষত্র। যখন একটি নক্ষত্রের জীবনকাল শেষ হয়ে যায়, তখন সেটা হয় সাদা বামন নক্ষত্র, নয়তো নিউটন নক্ষত্র, নয়তো কৃষ্ণগহবরে পরিণত হয়। তিনটির মধ্যে কোনটি ঘটবে, সেটা নির্ভর করে নক্ষত্রটির ভরের ওপর। এটা নিয়ে কার্ল সেগানের কসমস বইটির নবম অধ্যায়ে অত্যন্ত অসাধারণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। কসমস টিভি শোর সেই অংশটুকু নিম্নরূপ :
সূর্য, এক বিশাল সংযোজন চুল্লী, এর মধ্যে এঁটে যাবে এক মিলিয়ন পৃথিবী। সৌভাগ্যবশত, এর সঙ্গে আমাদের দূরত্ব ১৫০ মিলিয়ন কিলোমিটার। নক্ষত্রের নিয়তি কিন্তু বিস্ফোরিত হয়ে যাওয়া। রাতের আকাশে যে হাজার হাজার নক্ষত্র দেখেন, প্রত্যেকটিই দুটো বিস্ফোরণের মাঝে জিরোচ্ছে এখন। প্রথম বিস্ফোরণ হয় আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসের মধ্যে, নক্ষত্র তৈরি করার জন্য। এবং দ্বিতীয় বিস্ফোরণ- নক্ষত্রকে তার নিয়তির দিকে টেনে নেওয়ার জন্য। মহাকর্ষ নক্ষত্রকে সঙ্কুচিত হতে বাধ্য করে, যদি না অন্য কোনো বল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সূর্য একটা বিশাল গোলক, যা হাইড্রোজেন বিকিরণ করছে। এর অভ্যন্তরের উত্তপ্ত গ্যাস সূর্যকে বড় করতে চাইছে। আর মহাকর্ষ একে সংকুচিত করতে চাইছে। সূর্যের বর্তমান অবস্থা, এই দুই বলের ভারসাম্যে তৈরি। একটা সমতায় তৈরি, মহাকর্ষ আর নিউক্লীয় চুল্লীর মাঝে। দুই বিস্ফোরণের মধ্যকার দীর্ঘ বিরতিতে, নক্ষত্রগুলো বিরতিহীনভাবে আলো দিয়ে যায়। কিন্তু যখন নিউক্লীয় জ্বালানি ফুরিয়ে যায়, অভ্যন্তর ঠাণ্ডা হয়ে যায়, চাপটা বাইরের দেয়ালকে আর ধরে রাখতে পারে না তখন আগের বিস্ফোরণটা আবার শুরু হয়ে যায়।
তিনভাবে নক্ষত্রের মৃত্যু হতে পারে। তাদের নিয়তি আগেই লেখা হয়ে যায়। পুরোটাই নির্ভর করে এর প্রাথমিক ভরের ওপর। সাধারণ নক্ষত্র, যাদের ভর সূর্যের মতো, ওদের ধসে পড়া চলতে থাকবে, যতক্ষণ না উচ্চ ঘনত্ব অর্জন করছে। এরপর সংকোচন থেমে যাবে, কারণ কেন্দ্রে ভিড় করা ইলেকট্রনগুলো পরস্পরকে বিকর্ষণ করতে থাকবে। ধসে পড়তে থাকা নক্ষত্র যদি সূর্যের দ্বিগুণ হয়, সেটা ইলেকট্রনের বিকর্ষণে থামে না। এটা সঙ্কুচিত হতেই থাকে, যতক্ষণ না নিউক্লীয় শক্তি মাঠে নামে এবং সেটাই নক্ষত্রকে টিকিয়ে রাখে। কিন্তু ধসে পড়তে থাকা নক্ষত্রটা সূর্যের তিন গুণ হলে, নিউক্লীয় বলেও থামে না। এমন কোনো শক্তিই নেই, যা দিয়ে এই ভয়াবহ চাপকে বাধা দিতে পারবে। আর এ ধরনের নক্ষত্রের রয়েছে এক অভাবনীয় নিয়তি। এর সঙ্কোচন চলতে থাকে আর একসময় পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়।
নক্ষত্রের শ্রেণিবিভাগ করা যায় মহাকর্ষের বিরুদ্ধে কার্যরত বল দিয়ে। যে নক্ষত্র গ্যাসের চাপে টিকে আছে, সেটা স্বাভাবিক, গড়পড়তা নক্ষত্র, যেমন আমাদের সূর্য। ইলেকট্রনের বিকর্ষণে টিকে থাকা নক্ষত্রকে বলে সাদা বামন, এমন হলে সূর্যের আকার হয়ে যায় পৃথিবীর মতো। নিউক্লীয় বল দ্বারা টিকে থাকা নক্ষত্রকে বলে নিউট্রন তারকা, এমন হলে সূর্যের আকার হবে একটা শহরের মতো। আর নক্ষত্র যদি এত বড় হয় যে, ধসের পর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সেটাকে বলে কৃষ্ণগহ্বর।
সার সংক্ষেপ হলো—যদি প্রারম্ভিক ভর অত্যন্ত বেশি হয়, তাহলে ধ্বংসের মুহূর্তে (অর্থাৎ, নক্ষত্রটির জ্বালানি শেষ হওয়ার পর) নক্ষত্রটির মহাকর্ষ শক্তি যদি এতই প্রবল হয় যে, ওখান থেকে আলোও আর বের হতে পারে না, তখন সেটাকে আমরা বলি ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর।
কৃষ্ণগহ্বর ছোট হতে পারে আবার বড়ও হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্ষুদ্রতম কৃষ্ণগহ্বর একটি পরমাণুর সমান হতে পারে। এই জাতীয় কৃষ্ণগহ্বরগুলো অনেক ক্ষুদ্র কিন্তু তাদের একেকটির ভর হতে পারে বিশাল (ভর বিশাল, কিন্তু আয়তন নেই)। অন্য এক ধরনের কৃষ্ণগহ্বরকে বলা হয় ‘স্টেলার’ বা ‘নাক্ষত্রিক’; এর ভর আমাদের সূর্যের ভরের চেয়েও ২০ গুণ বেশি হতে পারে। খুব সম্ভবত অনেক অনেক বেশি ভরেরও নক্ষত্র রয়েছে আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথে। সবচেয়ে বৃহৎ কৃষ্ণগহ্বরকে বলা হয় ‘সুপারম্যাসিভ’; এই জাতীয় কৃষ্ণগহ্বরের ভর হয় এক বিলিয়ন সূর্যের ভরেরও অধিক। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, প্রতিটি বৃহৎ গ্যালাক্সি বা ছায়াপথের কেন্দ্রে এই রকম একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল থাকে। আর ছায়াপথের কেন্দ্রস্থলের এই কৃষ্ণগহ্বরগুলোকে বলা হয় Sagittarius A। এর ভর প্রায় চার বিলিয়ন সূর্যের ভরের সমান এবং এর ভেতরে আমাদের পৃথিবীর মতো কয়েক মিলিয়ন পৃথিবী অনায়াসে এঁটে যাবে।
জ্যোর্তিবিজ্ঞানীদের দুটি দল অস্ট্রেলিয়া ও চিলিতে ভূমিভিত্তিক টেলিস্কোপ ও হাবল মহাকাশ টেলিস্কোপ ব্যবহার করে পৃথিবীর মহাজাগতিক পরিমণ্ডলের কাছাকাছি তিনটি বিশালাকৃতির কৃষ্ণগহ্বরের সন্ধান পেয়েছেন। এর ফলে বিজ্ঞানীদের সামনে যে প্রশ্নটি এখন গুরুত্ব পাচ্ছে তা হলো ছায়াপথগুলোর আগেই কৃষ্ণগহ্বরগুলোর জন্ম হয়েছে কি না, যদিও ছায়পথের মধ্যেই কৃষ্ণগহ্বরের অবস্থান। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ভার্গো ও অ্যারিম নক্ষত্রপুঞ্জে নতুন তিনটি কৃষ্ণগহ্বরের অবস্থান জানা গেছে।
পিডিএসও/হেলাল